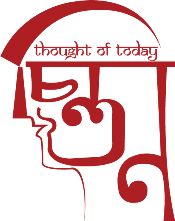শাশ্বতী ঘোষাল :চিন্তন নিউজ: ২৭ শে জুন:- বাংলা ভাষার যখন ঘোর দুর্দিন, যখন ইংরেজি শিক্ষিতদের কাছে বংলা ভাষা বর্বরের ভাষা, সংস্কৃতজ্ঞদের কাছে তা চণ্ডালের ভাষা ঠিক তখনই তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়ে আলোর কিরণে ভরিয়ে তুললেন সাহিত্য জগতকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। ……বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল” । সামগ্রিকতার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ। আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম।
বাংলায় উনবিংশ শতকের নবজাগরণের সমৃদ্ধ সময়ে তিনি একে একে রচনা করেছেন দূর্গেশনন্দিনী, রজনী, দেবী চৌধুরানী, কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর ,ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি প্রায় ষোলটি উপন্যাস। দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি নানান কালখণ্ডের পটভূমিতে তাঁর কাহিনীর বিন্যাস। অথচ তাঁর চরিত্রদের মনোজগতের বিবর্তন কিন্তু নিপুণভাবে তুলে আনছিল রেনেসাঁর অভিঘাতে টালমাটাল একটি জাতির পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিকের ছবি। যার মধ্যে প্রধানতঃ ছিল অগ্রসরমান আধুনিকতার স্পর্শে মেয়েদের মনস্তাত্বিক পরিবর্তনের দিকটা
রেনেসাঁর একটা প্রধান দিক ছিল মেয়েদের জীবনদর্শনে এক আমূল পরবর্তনের সূচনা, তাদের মধ্যে আত্মচেতনার জাগরণ, দোষে গুণে এক পরিপূর্ণ মানুষের ভূমিকার উন্মেষ, বঙ্কিমের নারী চরিত্রে সেই ক্রমবিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
নারীর শিক্ষিত মানসিকতার দিকে যে বঙ্কিমের আকর্ষণ তা তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর কল্প মানুষীরা আয়েষা, মেহেরউন্নিসা, মৃণালিনী, দলনী, চঞ্চলকুমারী, বিমলা সকলেই রাজঘরানার শিক্ষা সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। কপালকুণ্ডলা মন্দিরের অধিকারীর কাছে বাংলা, সংস্কৃত দুই ই শেখে। শান্তি ও দেবী চৌধুরানী দুই নায়িকা টোলে পাঠগ্রহণ করছে। ব্যাকরণ, সাহিত্য পাঠ তারা আয়ত্ত করছে মনোরমা পালকপিতার মুখে মুখে পুরাণ শাস্ত্র শিখেছে ইন্দিরা, দেবী চৌধুরানী, কপালকুণ্ডলা সকলের মধ্যেই সহজ সাহিত্য বোধ ও জীবন শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী ধারা প্রবহমান। সূর্যমুখী মিস টেম্পলের কাছে এবং রাধারাণী নব্যতন্ত্রের লোকের কাছে লেখাপড়া শেখে। সে সময়ের অন্তঃপুর ও যে নব্য শিক্ষার আলোয় প্রভাবিত হচ্ছে তার প্রমাণ ও দিয়েছেন তিনি।
তাঁর রচিত দূর্গেশনন্দিনীর আয়েষা চরিত্রটি মধ্যযুগীয় নারী চরিত্রের বদলে সম্পূর্ণ আধুনিক নারী হয়ে উঠেছে। ধর্ম, সমাজ ,সংসার কারো নিষেধাজ্ঞা সে মানে না। স্বধীনচেতা এক নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী হিন্দু সতীত্বের ধর্ম আত্মসুখবঞ্চনা কে একেবারেই মানতে রাজি নয়। সূর্যমুখী চিরাচরিত সংস্কারবদ্ধ স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও
তার মধ্যে দেখা যায় প্রখর আত্মসম্মানবোধ ।বহুগামী স্বামীর পদলুন্ঠিতা স্ত্রী হয়ে সে থাকে নি। বরং গৃহত্যাগের মত একটা সাহসী পদক্ষেপ সে নিয়েছে।
নারীর বিদ্যাকুতি ও ধী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় নারী পুরুষের সাম্য ও বঙ্কিমের রচনায় স্বীকৃতি পেয়েছে। সহশিক্ষার প্রতি সমর্থন ও ঠাঁই পেয়েছে তাঁর রচনায়। সাম্য প্রবন্ধে (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্কিম সহশিক্ষার পক্ষে স্পষ্ট অভিমত জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মেয়েদের ও ন্যায়শাস্ত্র পাঠ অবশ্য করা উচিত ,যা তখন নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েদের যুক্তিবাদী চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা গড়ে তোলা জরুরী তা যুক্তিবাদী বঙ্কিম সে যুগেই বুঝেছিলেন।
নরনারী নির্বিশেষে” আস্ত মানুষ ” হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে তিনি মনে করতেন। যে শিক্ষা কেবলমাত্র জীবিকামুখী, যে শিক্ষা পণ্ডিত, অহংবাদী ,অভিমানী করে তোলে, কল্যাণকর জীবন থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে সেই শিক্ষা নারী পুরুষ কারো জন্যই নির্দিষ্ট করা উচিত নয় বলে তিনি মনে করতেন।