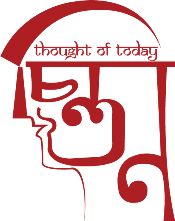চিন্তন নিউজ:৪ঠামে:-বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অধ্যাপক আবুল ফজল(১৯০৩,১লা জুলাই–১৯৮৩ ,৪ঠা মে) এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম ।তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার কেওচিয়া গ্রামের ভূমিপুত্র ছিলেন।পিতা ফজলুর রহমান এবং মা গুলশন আরার একমাত্র পুত্র আবুল ফজল মুক্তচিন্তার অগ্রপথিক হিশেবে বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিশেবে পরিগণিত।
ছেলেকে নিয়ে বাবা ফজলুর রহমানের ইচ্ছের শেষ ছিল না। সেই সব ইচ্ছের ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল তিনটি। প্রথমতি হল; ছেলে যেন সারা জীবন দাড়ি রাখে।
দ্বিতীয়টি হল , ছেলে পড়াশুনা করলেও যেন লেখালেখি তে নিজেকে সংযুক্ত না করে।যদি সে শেষ পর্যন্ত লেখালেখি করেও , তাহলে কোনো অবস্থাতেই বাংলাতে যেন না করে।যদি শেষ পর্যন্ত লেখেই , তবঃ যেন ফার্সি, উর্দু কিংবা আরবিতে লেখে।
তৃতীয়ত, শিক্ষকতা হল পেশা হিশেবে সবথেকে ভালো।ছেলে যেন শিক্ষক হয়।শিক্ষকতাকেই পেশা হিশেবে বেছে নেয়।
বাংলার দ্বিতীয় জাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ আবুল ফজল তাঁর বাবার এই দ্বিতীয় কথাটি কোনো অবস্থাতেই রাখেননি। প্রথম ও শেষ কথা টি রেখেছালেন।। আবুল ফজল বাংলা ভাষাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। ফার্সি, আরবি কিংবা উর্দু বুঝতেন, সেই ভাষাতে লিখতে বা পড়তেও পারতেন
কিন্তু সেই ভাষাকে কখনো মন থেকে নিজের করে নিতে পারেন নি ।
পিতার প্রতি সম্মান, মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধা তাঁর কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু নিজের লেখালেখিতে, যাপনচিত্রে বাংলা ভাষা ত্যাগ করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না।
আরো একটি জিনিস বাদ দিয়েছিলেন।সেটি হল, মোহাম্মদ। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ আবুল ফজল। পিতার রাখা নামের প্রথম শব্দ বাদ দিয়ে তিনি মোহাম্মদহীন, অর্থাৎ; শুধু ‘আবুল ফজল’ হিশেবেই নিজেকে পরিচিত করেছিলেন।
সেইসময়ের বাঙালি প্রগতিশীল মুসলমানদের যেসব মৌলিক সমস্যা সহজে দেখতে পাওয়া যেত, সেইসব সমস্যাগুলির বেশির ভাগের ভিতর দিয়েই আবুল ফজল কে পারিবারিক জীবনের প্রথমক্রম টি কাটাতে হয়েছিল। বাবা ফজলুর রহমান বাংলা ভাষাকে নেতিবাচক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করতেন। অথচ কথা বলতেন বাংলাতেই। ধর্মীয় রীতিনীতিতে তিনি ছিলেন বেশ রক্ষণশীল। যদি ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রতি ছিলেন উদার। পরোপকারী।কোনো রকম বিবাদ- বিসংবাদ প্রতিবেশি হিন্দুদের সাথে আবুল ফজলের বাবা ফজলুর রহমানের ছিল না।
এই যে বাংলা ভাষাকে ঘিরে একটা নেতিবাচক মানসিকতা, সেটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিল, আত্মপরিচয়ের টানাটানি। মানুষ হিসেবে চাইতেন তিনি মানুষের মত করে ই, মানুষের ভিতরেই বসবাস করতে। কিন্তু ধর্ম তাতে প্রধান বাঁধা হিশেবে উপস্থিত হতো।তিনি কিবাঙালি? নাকি তিনি মুসলমান? আত্মপরিচয় নিয়ে এই রকম একটা গভীর- জটিল টানাপোড়েনের ভিতরেই মনীষী আবুল ফজলের বেড়ে ওঠা।
১৯০৩ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণে কেঁওচিয়া নামের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর জন্ম কার্যক্রম ছিল তাঁদের পরিবার – পরিজনের জন্য বিশেষ আনন্দের। কারণ, তাঁদের পরিবারে তিনিই ছিলেন প্রথম পুত্র সন্তান। শেষ পর্যন্ত আবুল ফজল প্রথম এবং একমাত্র পুত্র সন্তান হিসেবেই থেকে গেলেন। আদরের পুত্র সন্তান হিশেবে যে পারিবারিক প্রশ্রয় তিনি পেয়েছিলেন, সেটিকে নিজের বিবেকের উন্মীলনে ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন আবুল ফজল।
তাঁর বাবা চাইতেন মৃত্যুর পর তিনি যেন তাঁর ছেলের ভিতরে বেঁচে থাকতে পারেন। ছেলে যেন তাঁর মতই ধার্মিক, পরহেজগার ও দ্বীনের পথের যাত্রী হয়- এটাই ছিল তাঁর পিতার শেষ ইচ্ছা তাই নিজের ভিতরে যত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কট্টরপন্থা ছিল, সেই সবটুকু ছেলের মনে দেগে দিতে চেয়েছিলেন ফজলুর রহমান। তাঁর পিতার কাছ থেকে ফজলুর যে রক্ষণশীলতা পেয়েছিলেন, সেটিকেই তিনি চেপে বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন প্রিয় পুত্রের ভিতরে। আবুল ফজলের পিতামহ ছিলেন আলেম, সেই সূত্রে পিতাও ছিলেন আলেম। বংশ পরম্পরা কে এই ভাবেই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন আবুল ফজলের পিতা।তাই ছেলের বাল্যকাল থেকেই সন্তানকে ধর্মমন্ত্রে বশ করতে চাইতেন।
অথচ মনীষী আবুল ফজল পরিবার পরিজনের আদরটুকু চেয়েছিলেন।পরিবার- পরিজনের চাপিয়ে দেয়া ধর্মীয় গোঁড়ামি টাকে কোনো অবস্থাতেই চাননি। তাই তিনি সব সময়েই মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। স্বাধীনচেতা মন নিয়ে ছোট থেকেই চলেছেন তিনি।সব সময়েই নতুন চিন্তা ও বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখাটাই তিঁর মননলোক বিকাশের প্রাথমিক লক্ষণ হিশেবে ফুটে উঠতে শুরু করেছিল তাঁর শৈশব থেকেই।
এইসব স্বত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে , যে সময়কালটাতে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমান সমাজ, তাঁদের ‘মুসলমান’ শব্দ টির ভিতরেই আত্মপরিচয় খুঁজে বেড়িয়ে তৃপ্তি লাভে ব্যস্ত থেকেছে, সেইসময়কাল টাতে আবুল ফজলের জন্য মুক্তির স্বাদ পাওয়া ছিল বেশ কঠিন বিষয়। কিন্তু এইরকম একটা সামাজিক কঠিন পরিস্থিতিকে জয় করাই ছিল আবুল ফজলের চরিত্রের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্র।নিজের প্রবল আত্মমর্যাদা, বিবেক এবং সম্ভ্রম দিয়েই সেই সামাজিক কাঠিন্য কে সহজ করে নিতে মনীষী আবুল ফজল সক্ষম হয়েছিলেন। এই সাফল্যের পিছনে কিন্তু তাঁর বাবা ফজলুর রহমানের পরোক্ষ সহায়তা আছে।সেই সহায়তার কথা আবুল ফজল পরবর্তী জীবনে খুব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন।
আবুল ফজলের পিতা ফজলুর রহমান থাকতেন শহরে।শিশু আবুল ফজল তাঁর মা গুলশন আরার সঙ্গে গ্রামে থাকতেন। গ্রাম মানে , সেটা ছিল সবদিক থেকেই আদর্শ গ্রাম। বড় বড় পুকুর,বিশাল উঠোন ,বাড়ির পাশে সুবিশাল মাঠ, মাঠে গরু আর দামাল ছেলের পাল। উঠানে, পুকুরে, মাঠে আবুল ফজলের বাধাহীন ছুটোছুটি। ঘন্টার পর ঘন্টা পুকুরে স্নান,সাঁতার।
মায়ের বারবার ডাকাডাকির পর পুকুর থেকে উঠতেন। কিন্তু উঠলেন, ওই পর্যন্ত!বাড়ি মুখো হতেন না।পুকুর থেকে উঠেই চলে যেতেন মাঠে। নিজেদের গবাদিপশু ছিল না। বাড়ির পাশের কারো না কারুর তো ছিল।প্রতিবেশীদের গরু নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। এই রকম খোলামেলা প্রকৃতি ও সরল স্বাধীন বাল্যকাল ই মনীষী আবুল ফজলের যৌবনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।
এই পর্যায়ক্রমের প্রভাবেই তিনি তাঁর বাবার মত ইসলামের খাদেম হওয়ার পাশাপাশি একজধ মুক্তবুদ্ধির সমাজ সংস্কারকও হতে পেরেছিলেন।এই রকম স্বাধীনতার ভিতরে খারাপ সময় ততটুকুই , যতটুকু সময় বাবা ফজলুর রহমান বাড়িতে থাকেন।পবিত্র ইসলামের হুকুম আহকাম, মাসলা মাসায়েল – বাবা বাড়ি আসতেন এই সব কিছু নিয়ে। ধর্মের বাড়াবাড়ি, গোঁড়ামি ছিলো সত্যি; ছেলেকে আলেম বানাতে চেয়েও ছিলেন পিতা, এটাও সত্যি। কিন্তু নির্বোধ বানাতে তিনি চাননি। ছেলের শিক্ষাগ্রহণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বেশি রকমের যত্নবান ছিলেন। তাঁর পিতা চাইতেন ছেলে যথার্থ শিক্ষিত হোক। আবুল ফজলের লেখাপড়ার পথ খুব একটা মসৃণ ছিল না।তাঁকে ইস্কুল, মাদ্রাসা, আবার ইস্কুল, আবার মাদ্রাসা- এই ঘুরপাকে থাকতে হয়েছিল। এই রকম করতে গিয়ে প্রায় দুই বছর সময় তাঁর ক্ষতি হয়ে গিয়ৈছিল। তিনি লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। তাঁর বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন ছেলের জন্য চাকরি নিয়ে। আর চাকরি নিয়ে আবুল ফজল বিব্রত হতে থাকেন বয়স ঘিরে। এই বয়সের কারণেই ইস্কুল- কলেজে , কোনো জায়গাতেই তিনি বৃত্তি পাননি।এমন কি সরকারি চাকরি ও পান নি।। তাই সরকারি চাকরির প্রত্যাশা ছেড়ে দিয়েই করে প্রথমে আইন ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন, পরে শিক্ষকতা। পিতা প্রথমে তাঁকে ভর্তি করিয়েছিলেন গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলে । গাঁয়ের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ার পর বাবার সঙ্গে চট্টগ্রামে চলে আসেন। পিতার ইচ্ছে ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করাবেন। কিন্তু মাদ্রাসা বর্ষ( সেশন) শুরু হতে কিছুদিন দেরি আছে তখন।তাই বাড়ির কাছাকাছি নন্দন কানন নামক একটি জায়গার প্রাইমারি ইস্কুলে তিনি ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯১৩ সালে আবুল ফজল চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসাটি ছিল সাবেকী মাদ্রাসা। আরবি ও ফার্সি ভাষার পাঠক্রম। আবুল ফজল অনেকটাই হতাশ। কয়েকদিন পর তিনি যে মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়েছিলেন , সেই মাদ্রাসাটি ,নিউ স্কীম মাদ্রাসায় রূপ নেয়। পুরোনো পাঠক্রম বাতিল হয়ে যায়।সমন্বিত পাঠক্রম চালু হয়। সঙ্গে যুক্ত হয় ইতিহাস ও আধুনিক ভুগোল শিক্ষা। ফার্সি ভাষা সম্পূর্ণরূপে বাদ যায়। কিছুটা ইংরেজি, কিছুটা বাংলা এবং অংক যুক্ত হয়। পাঠদানে বাংলা ভাষা নিরঙ্কুশ আধিপত্যছিল না। যদি ও সেই মাদ্রাসায় নিয়মিত বাংলা মাসিক পত্রিকা ও লাইব্রেরিতে বেশ কিছু বাংলা বই নেয়া হতো।একটা সময়ের অপ্রিয় মাদ্রাসা এবার খুব প্রিয় হয়ে ওঠে আবুল ফজলের কাছে।একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি ভাবে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্টের অদল বদলের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের কাছে খুব কাছের হয়ে ওঠে, সেটা বোঝাতে পরবর্তীকালে নিজের জীবনের এই ঘটনিবলীর কথা খুব জোরের সঙ্গে আবুল ফজল বলতেন।এইসময়েই আবুল ফজলকে নতুন কিছু সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। বাবার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তাঁকে জায়গির থাকতে হয়। সেইসময় জায়গির থাকার বেশ প্রচলন ছিল। এই বিশ শতকের সূচনা লগ্নে জায়গির থাকার বিষয়টি কিন্তু বাংলার সামাজিক জীবনকে বেশ প্রভাবিত করেছিল।দুঃখের বিষয়, আর্থিক কারণে কিছু কিছু পরিবারের পুরুষদের এই অন্য পরিবারে জায়গীর থাকার বিষয়টি এপার বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের একদম ই চোখ এড়িয়ে গেছে।ফলে আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এপার বাংলার পাঠকদের কাছে প্রায় অজানাই থেকে গেছে।অন্যের বাড়িতে থেকে খেয়ে লেখাপড়া করবে, বিনিময়ে সেই বাড়ির বাচ্চাকাচ্চাদের পড়াবে। বর্তমান সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকার বিনিময়ে পড়ানোর রীতি থাকলেও জায়গিরের রীতি নেই বললেই চলে। এমনকি গ্রামেও এই রীতি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় অবলুপ্ত।আবুল ফজল যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তখন বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুলের বেশ সুনাম দিগন্ত বিস্তৃত। মাসিক পত্রিকাগুলোয় নজরুলের লেখা ছাপা হয়। আবুল ফজল দুই একটা লেখা পড়েই নজরুলের প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন নজরুলের পরপর দুটি বই বের হয়। ‘ ব্যাথার দান ‘ আর ‘ অগ্নিবীণা’ ।
জমানো টাকার সবগুলো দিয়ে কলকাতা থেকে বই দুটি পার্শ্বেলের ব্যবস্থা করেন। এই খবর বন্ধুমহলে ছড়িয়ে পড়লে সবাই অবাক হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের কাছে তখন শুধু শখের বশে এত দূর হতে বই আনানো খুব সহজ কথা ছিল না। বইগুলো হাতে পেয়ে আবুল ফজল যেন নেশামগ্ন হয়ে পড়েন। এরপর তিনি আরো বই আনান। মাসিক পত্রিকাগুলোয় নজরুলের লেখা নিয়মিত পড়তে শুরু করেন। মূলত নজরুলের লেখা পড়ে আবুল ফজলের লেখালেখির ইচ্ছে তৈরি হয়েছিল।সেই ইচ্ছেকেই পরবর্তীকালে নিজের জীবনের অন্যতম ব্রতে তিনি পরিণত করেছিলেন।আবুল ফজলের বাবা তখন চট্টগ্রাম জামে মসজিদের ইমাম। একদিন খুব আশা নিয়ে ইমাম সাহেবের দ্বাদশ শ্রেণি পড়ুয়া ছেলে মহম্মদ নাসিরুদ্দিনের ‘ সওগাত’ পত্রিকায় লেখা পাঠান। লেখাটি ছাপাও হয়। কিন্তু লেখকের আগে সেই লেখা পড়েন স্থানীয় হাইস্কুলের এক শিক্ষক। পরিচিত তরুণের লেখা বিখ্যাত পত্রিকায় পড়ে সেই শিক্ষক যার পরনাই খুশি।তিনি ভাবলেন তরুণ লেখকটির বাবাও নিশ্চয় খুশি হবেন। এই ধারণা থেকেই তিনি খবরটি আবুল ফজলের বাবাকে জানালেন।জানানোর সাথে সাথেই বিপর্যয়। ইমাম সাহেব ভয়াবহভাবে বিরক্ত হলেন, সীমাহীন ক্রোধান্বিত হলেন, বিব্রত বোধ করলেন। কজন ইমামের ছেলে কিনা বাংলা ভাষার পত্রিকায় কীসব লিখেছে? এই চিন্তা তাঁকে ভীষণ বিব্রত করল।তিনি ভাবলেন , মান সম্মান বোধ হয় আর রইলো না। বসে রইলেন ছেলের অপেক্ষায়। ছেলেও কী এক প্রয়োজনে বাবার সাথে দেখা করতে এলো। ব্যস্! রুদ্র রুক্ষ মূর্তিমান বাবার সামনে পড়তেই ধমকের সুরে প্রশ্ন গিলতে হলো। তুমি নাকি বাংলা পত্রিকায় লেখা শুরু করেছ? – এমন প্রশ্নের জবাবে প্রথমে মনে মনে খুব খুশি হয় আবুল ফজল। বুঝতে পারলেন নিশ্চয় তার লেখা সওগাত পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু বাবার সামনে খুশি লুকিয়ে রেখে সরাসরি অস্বীকার করলেন। বাবা বললেন “হাই স্কুলের শিক্ষক নিজে এসে আমাকে বলে গেছেন, এমনকি তিনি লেখাটি পড়েছেনও! আবুল ফজল নামে প্রকাশিত হয়েছে।” আবুল ফজলের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল বেশ তীক্ষ্ণ। দ্রুত বলে দিলেন, “আমার নামতো মোহাম্মদ আবুল ফজল। আবুল ফজল নামে যিনি লিখেছেন, তিনি নিশ্চয় অন্য কেউ হবেন।” যুক্তিটা যেহেতু মোহাম্মদ নিয়ে, বাবা সহজে বিশ্বাস করলেন। এই ভাবেই আবুল ফজল ইন্টারমিডিয়েট শেষ করলেন। কিন্তু সরকারি চাকরি তিনি পেলেন না। এই সরকারী চাকরি পেলেন না, কেবলমাত্র বয়সের কারণে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে ১৯২৮ সালে বি. এ. পাশ করলেন। এরপর এলএলবি পড়ে ওকালতি পেশায় যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে তৈরি হল তাঁর । বাবাকে নিজ ইচ্ছের কথা বললেন। বাবা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন ছেলের কথা।কারণ, বাবার ধারণা উকিলরা প্রচুর মিথ্যা বলেন। ফজলুর রহমান চাননি তাঁর ছেলে মিথ্যার পেশায় যুক্ত হোক। আবুল ফজলের বাবা নিজে মিথ্যা বলতেন না, যাঁরা মিথ্যা বলে, তাদেরকে তিনি একদমপছন্দ করতেন না।অথচ পুত্র আবুল ফজল ওকালতি পেশায় যুক্ত হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। গ্রামে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ল’ পড়তে কলকাতায় পাড়ি জমালেন। আবুল ফজল ভেবেছিলেন, হয়তো ছেলের জিদের কাছে পিতা হার মানবেন। কিন্তু তাঁর বাবা নিজের বিবেচনাপ্রসূত চিন্তায় চোর, ডাকাত, ভালো, মন্দ সবার স্বার্থ দেখার পেশায় ছেলে যুক্ত হোক, এটা কোনভাবেই চাননি। এদিকে তার ছেলে কলকাতায় সীমাহীন অর্থকষ্টে জোড়াতালি দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকমাস পর শুনতে পেলেন বাবা অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছেন। সবকিছু বন্ধ রেখে বাবাকে দেখতে আসলেন। বাবার বিছানার কাছে গিয়ে সে একই কথা শুনলেন। “উকিল হইও না, শিক্ষক হও। শিক্ষকতার চেয়ে মহৎ পেশা আর নাই।”
তারপর বাদ দিলেন। বাবার কথা রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছায় নতুন করে লেখাপড়া শুরু করলেন। এর মধ্যে ১৯২৯ সালে তার বাবা মারা যান। ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে বি.টি. ডিগ্রী শেষ করে ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। যোগ দিলেন শিক্ষকতায়। প্রথমে স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় মৌলবী হিসেবে, পরে চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে, এরপর চট্টগ্রাম কাজেম আলী বেসরকারী হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে অস্থায়ীভাবে যোগ দেন আবুল ফজল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পড়ার সময়ে ই বাংলার দ্বিতীয় জাগরণের কর্মবাহী ‘ মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৬ সালে মুসলমান সমাজে বুদ্ধির মুক্তি আনার উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের একটি অংশ মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।সেই বছর তারা ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’ স্লোগান ধারণ করে প্রকাশ করলেন। সমাজ সংস্কারমূলক সেই পত্রিকা র নাম হল,’ শিখা।’ এই উদ্যোগের সাথে জড়িতরা সবাই শিখাগোষ্ঠী নামে পরিচিতি লাভ করেন।অন্নদাশঙ্কর রায় এই গোটা কর্মকান্ডকে ,’বাংলার দ্বিতীয় জাগরণ ‘ বলে অভিহিত করে গিয়েছেন।বস্তুত, উনিশ শতকের বাংলাতে হাজি মহঃ মহসিন , রামমোহন রায়, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় , শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ – প্রমুখ যে নবজাগরণ এনেছিলেন, এটি যেন সেই নবজাগরণকেই একটা সুনিবিড় পরিপূর্ণতা দিয়েছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের এই ‘ শিখা’ গোষ্ঠীর সকল দীপ্যমান ‘ শিখা’ র ভিতরে , স্বীকার করতেই হয় মনীষী আবুল ফজলের জ্বালানো ‘ শিখা’ র আলো কিছুটা হলেও অস্পষ্ট ছিল।অনেক ক্ষেত্রেই সেই আলোকবর্তিকা বেশ বিভ্রান্তিকর ও ছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামক সংগঠনে আবুল ফজলের অংশগ্রহণ ছিলো প্রশ্নাতীত। তবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের সংস্কার কাজে তিনি অন্যদের মত স্বচ্ছ ছিলেন না– এইকথা স্পষ্ট ভাবেই বলা যায়। ১৯২৯ সালে মনীষী কাজী মোতাহার হোসেন সম্পাদিত ‘শিখা’র তৃতীয় সংখ্যায় ‘তরুণ আন্দোলনের গতি’ নামে আবুল ফজলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধটি পড়লেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্য সদস্যদের সাথে আবুল ফজলের ভাবনার মৌলিক ফারাক টা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারা যায়।সেই প্রবন্ধে আবুল ফজল লিখছেন;
” অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে সত্যের পথে টানিয়া লইয়া যায়। বিশ্বাস করিয়া মানুষের সুখ আছে জানি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানে বা সত্যকে আবিষ্কার করিয়া মানুষের যে সুখ, আত্মপ্রসাদ —তাহার তুলনা নাই। সন্দেহই জ্ঞানের গোঁড়া —এইতো বড় বড় দার্শনিকের কথা। সন্দেহ হইতে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে। এই অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে জ্ঞানের পথে চালিত করে। আজ মুসলমান ছেলের মনে জীবনের বড় কিছু সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে পারে না। সন্দেহ জাগিলে তাহার গলা টিপিয়া ধরা হয়। …পিতা পিতামহ বিশ্বাস করেন, খোদা এক। ধর্মশ্রাস্ত্র বলে খোদা এক। ব্যাস, আমি বিশ্বাস করি —খোদা এক। এইতো আমাদের জ্ঞান। কিন্তু খোদা নাই বা খোদা একাধিক, এই সন্দেহ কোন মুসলমান ছেলে প্রকাশ করিলে তাহার কি আর নিস্তার আছে।”
‘ শিখা’ তেই তিনি অকপটে লিখেছেন; “বহুদিন হইতে দেশে অসংখ্য মাদ্রাসা চলিয়া আসিতেছে এবং বছর বছর তাহা হইতে অসংখ্য ছাত্র পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। শরিয়তের সব কিছুই তো এখানে পড়ায় না। তথাপি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহারা নতুন কিছু দান করিতে পারিতেছেন না কেন? শরিয়তের বিধিনিষেধগুলিরও আধুনিক জীবনের মতবাদ অনুযায়ী ইহারা কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না কেন? ইহার উত্তর, —ইহাদের মনে জ্ঞান ও চিন্তার গোড়া সন্দেহ জাগিতে পারে নাই। …তাহাদর মনে এই শিক্ষা ও সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দেওয়া হয় যে এই আরবি ফারসি কেতাবে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহা অলঙ্ঘনীয় সত্য। ইহার কোন বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের স্থান নহে। যাহার মনে সন্দেহ জাগে, সে গুনাহার। এমনি করিয়া মুসলমানের জ্ঞানের উৎসকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।” এই প্রবন্ধের শেষে আবুল ফজল লিখছেন;”হিন্দু যদি আজ সমুদ্রযাত্রাকে অধর্ম ভাবিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, অথবা খ্রিস্টান যদি আঘাতের প্রতি আঘাতের পরিবর্তে অন্য গালখানি পাতিয়া দিত, তাহা হইলে তাহাদের জায়গা স্বর্গে হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এই মাটির দুনিয়ায় একেবারে অসম্ভব হইত। মুসলমানকেও যদি দরকার হয় এইরকম নির্মমভাবে সামাজিক বিধি নিষেধকে পরিবর্তন করিতে হইবে। ইসলামের মূল সূত্রকে পরিবর্তন করিতে বলিতেছি না এবং তাহার দরকারও নাই।” মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ‘ শিখা’ র যে সংখ্যাতে আবুল ফজলের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাটির সম্পাদক ছিলেন মনীষী কাজী মোতাহার হোসেন ।আবুল ফজলের লেখার এই অংশের শেষে একটা তারকা চিহ্ন তিনি বসিয়েছিলেন।সেই তারকা চিহ্নের ভিতর দিয়ে প্রবন্ধের শেষে পাদটীকায় প্রবন্ধটির লেখক আবুল ফজলকে টিপ্পনি কেটে কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছিলেন;– ” লেখকের শোষোক্ত বাক্যটির তাৎপর্য কি বুঝিলাম না। পাছে তওবা করিতে হয় সেই ভয়ে কি এ বাক্যটি লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলমের আগায় বাহির হইয়াছে? তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে এই বাক্যটি খাপ খাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।” কাজী মোতাহার হোসেনের এই বিশেষ বক্তব্য থেকে এটা খুব ভালোভাবে পরিস্কার হয়ে যায় যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে মুসলমান সাহিত্য সমাজ এবং শিখা গোষ্ঠী কতোখানি পরিচ্ছন্ন ছিলেন।আজকের দিনে হলে, পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর অভিমতের বিপক্ষে কোনো ভিন্ন ভাবনার লেখা , ছাপাই হতো না।’ শিখা’ তে কিন্তু অমন টা কিছুই ঘটে নি।ভিন্ন রুচির অধিকারের স্বীকৃতির প্রশ্নে এই উন্নত চিন্তা কিন্তু আজকের দিনে দুই বাংলার কোথাও ই একটুকুর জন্যেও ভাবতে পারা যায় না। আবুল ফজল কিন্তু ধর্মের প্রসঙ্গে একটা ভালো রকমের দোটানায় ভুগতেন।অনেক সময়েই তিনি প্রগতিশীল সংস্কারবাদীর তালিকায় থাকতে চাইতেন ।আবার ধর্মপ্রেমিদের তালিকা থেকে ও নিজেকে বিযুক্ত করতে চাইতেন না।এই রকম একটা ভয়ঙ্কর রকমের দ্বৈততা আবুল ফজলের জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক চিন্তায় দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছিল।
জীবনের শেষ পর্যন্ত এই দ্বেততার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন। যা হোক, এই ‘শিখা’ পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। আবুল ফজল এই সংখ্যার সম্পাদনা করেন। এরপর পত্রিকাটির আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।
ইতিহাস বলে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান সমাজে একসময় ব্যাপক উর্দুপ্রীতি ছিলো। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর এই প্রেমে নতুন জোয়ার আসে। পঞ্চাশে যখন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন রচিত হয় তখন মুসলমান সাহিত্যিকদের মাঝে অনেকে নতুন করে উর্দুর প্রেমে সিক্ত হন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় বাংলা লেখক উর্দুর পক্ষে অবস্থান নেন, যাদের মাঝে কবি গোলাম মোস্তফা অন্যতম। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি আবুল ফজলের প্রেমে কখনোই ভাটা পড়েনি। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি বাংলার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এবং উর্দুর পক্ষ নেয়া শিক্ষক সমাজের সাথে সম্মুখ তর্কে লিপ্ত হতেন।কিন্তু একই সময় আবার ব্যক্তিস্বার্থে উর্দুপ্রেমী সাহিত্যিকদের সাথে জোট বেঁধে মুসলিম সাহিত্য সমাজের অগ্রজ সহযোদ্ধা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে অপ্রত্যাশিত বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। সেই বিবাদ – বিসংবাদ ছিলো বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চেতনাবিরোধী এবং স্পষ্টভাবে স্ববিরোধী। আবুল ফজল জীবনভর এরকম বেশকিছু স্ববিরোধী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হন, যার মূলে ছিলো ব্যক্তিস্বার্থ অথবা ব্যক্তিগত বিরোধ।
১৯৫২ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লেকচারার থেকে প্রফেসরে উন্নীত হন। একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ শুরু করেন। এসময় সিলেবাস প্রণয়ন নিয়ে বিতর্কে বাংলাপ্রেমী আবুল ফজল আর উর্দুপ্রেমী কবি গোলাম মোস্তফা যৌথভাবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসেন। শুধু এই দু’জনই নন, এই আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আর ও বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক, যাঁরা আশা করেছিলেন সদ্যজাত পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে তাঁদের নিজেদের সাহিত্যকর্ম স্থান পাবে।
কিন্তু দেশ ভাগের পাঁচ বছর পরও নিজেদের লেখা পাঠ্য তালিকায় না দেখে এইসব সাহিত্যিকেরা দুঃখ পান এবং নতুন বিভাগীয় প্রধান শহীদুল্লাহকে নিশানা করে প্রতিবাদের আওয়াজ তোলেন। যদিও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে লক্ষ্য করে আক্রমণ অযৌক্তিক ছিল। কারণ; দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি নতুন পাঠক্রম তৈরিতে হাত দেন এবং সেই কাজ তখনো শেষ না হওয়ার জন্যে অন্য দিকে তিনি মনোনিবেশ করতেই পারেন নি। আবুল ফজল ১৯৪৮ সালে ‘জিন্দেগী’ পত্রিকায় ‘সিরাজুল ইসলাম’ ছদ্মনামে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান-বিরোধী মনোভাব’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন।পরবর্তীতে এই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ একটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কোন মুসলমান অধ্যাপক নিয়োগ না দেয়া, হিন্দু লেখকদের লেখা কমিয়ে না আনা, মুসলমান লেখকদের রচনা অধিকভাবে যুক্ত না করাসহ আরো কিছু হিন্দু বিদ্বেষী অথবা মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। সেখানে ড. শহীদুল্লাহকে মুসলমান বিদ্বেষী এবং ভারতপ্রেমী আখ্যা দেন। এই প্রবন্ধে যেসব লেখকদের লেখা যুক্ত না হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে আবুল ফজল রচিত নাটক ‘কায়েদে আজম’ ও গোলাম মোস্তফা রচিত ‘বিশ্বনবী’ অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের আধিক্য আবুল ফজল পছন্দ না করলেও তিনি বেপরোয়া ভাবে হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন , এমন টা কিন্তু নয়। তবে নিজ ধর্মীয় সমাজের স্বার্থের দেখভাল করতেন। আবুল ফজল দারুণভাবে রবীন্দ্রপ্রেমী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে আইয়ুব খানের সরকার যখন রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তান আদর্শের পরিপন্থী বিবেচনা করে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।
কর্মজীবনের অধিককাল পর্যন্ত আবুল ফজল শিক্ষকতা করেছেন। পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শেষে ১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা বিষয়ের লেকচারার পদে যোগ দেন। এরপর ১৯৪৩ সালে বদলি হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে আসেন। ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগদান করেন।
এসময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যার সূত্রপাত হয় ড. নীলিমা ইব্রাহিমকে বাংলা একাডেমির মহা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে। বাংলা একাডেমি তখন নানান অনিয়মের ভারে জর্জরিত। যুদ্ধ পরবর্তী নারী পুনর্বাসন কাজে নীলিমা ইব্রাহিমের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার কারণে তার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই আস্থা থেকে তাকে রুগ্ন বাংলা একাডেমিকে সুস্থ করার দায়িত্ব দেন। কিন্তু বিষয়টি পছন্দ হয়নি আবুল ফজলের। তিনি ‘বিচিত্রায়’ কলাম লিখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখেন, “কেন একজন মেয়েমানুষকে বাংলা একাডেমীর ডি.জি., বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান, রোকেয়া হলের প্রভেষ্ট ও মহিলা সমিতির সভানেত্রী করা হয়েছে?”
অথচ এই আবুল ফজলই ১৯৩১ সালে ‘শিখা’ পত্রিকায় লিখেছিলেন —
মেয়েদের শিক্ষা, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালি-মুসলমান সমাজে বহুদিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু আমাদের সমাজনেতারা শুধু বাক্যের ব্যবসাদারিতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া নিজেরা ফতুর হইতেছেন এবং সমাজকেও বিড়ম্বিত করিতেছেন। Example is better than precept, একথা তাঁহারা বুঝিতেছেন না, বা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া মনে করিতেছেন আমরা সমাজের নেতা, সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত pioneer — ইয়া উয়া! আজ এই ঢাকা সাহিত্য সমাজের সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্ব স্ব পরিবারের মহিলাদের এই সভায় যদি লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে এই আন্দোলন আজ একদিনে অন্তত আরো দশ বৎসর আগাইয়া যাইতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহাদের যে নাড়ির যোগ রহিয়াছে, তাহাও প্রমাণিত হইয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ আমরা তাহার উল্টা দেখিতেছি।
আবুল ফজল এমনই ছিলেন। যখন তার কোন কিছু পছন্দ হয়নি, কিংবা নিজ স্বার্থে আঘাত লেগেছে, তখনই তিনি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতেন, নারী প্রগতি বিদ্বেষী হয়ে উঠতেন। সে বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটেসেটি সদ্য স্বাধীন এবং দুর্ভিক্ষ ক্লিন্ন বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এই সময় কালেই এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষক সমাজের সমালোচনা করে কিছু কথা বলেন। আবুল ফজল ভেবেছিলেন এই কথাগুলো ফল বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কারণ তিনি সেই সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। অপমানবোধে জর্জরিত হন আবুল ফজল।তিনি ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের জবাব দেন এবং তীব্র সমালোচনা করেন। এই ঘটনাটি তৎকালীন সরকার ভালোভাবে নেয়নি। ফলে তাঁর কাজকর্মে বেশ চাপ সৃষ্টির অভিযোগ ওঠে। কিন্তু আবুল ফজল তাঁর কথা থেকে এক বিন্দু পরিমাণও সরে যাননি। তিনি অটল ছিলেন নিজের কথাতে। আবুল ফজলের এই মন , আপসহীনতা, এই জন্য তখনকার বুদ্ধিজীবী সমাজ আবুল ফজলকে ‘জাতির বিবেক’ হিসেবে আখ্যায়িত করে।
কিন্তু পঁচাত্তরের শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যার পর পর তাঁর বিবেক যথেষ্ট নড়বড়ে হয়ে যায়। জিয়াউল হক, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের পরিণতি খুব কাছ থেকে দেখা আবুল ফজল ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে সামরিক সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ১৯৭৭ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত তিনি এই পদে কর্মরত ছিলেন। খুনী মেজর চক্রের সাথে তাঁর এই আপোষের বিষয় টি কে বাঙালি ভালোভাবে নেয় নি।
এই কালের সমালোচক হুমায়ুন আজাদ আবুল ফজলকে নিয়ে একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন। যে মন্তব্যটি বর্তমানে প্রবচন হিসেবে বহুল ব্যবহৃত।সেটি হল,বাঙলার বিবেক খুবই সন্দেহজনক। বাঙলার চুয়াত্তরের বিবেক সাতাত্তরে পরিণত হয় সামরিক একনায়কের সেবাদাসে।
আবুল ফজল কোন মহামানব কিংবা ঐশী শক্তি সম্পন্ন কেউ ছিলেন না। ছিলেন না রাগ, ক্ষোভ, লোভ ও মোহের উর্ধ্বের কোনো মানুষ। দোষ ও গুণের মিশেলে একজন সাধারণ মানুষ , অথচ গড়পড়তা থেকে অনেক উঁচু স্তরের ছিলেন। তাঁর বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি প্রেম ও পরিশ্রম তাঁকে অসাধারণ করে তুলেছে। সব থেকে বড়ো কথা আবুল ফজল ছিলেন বাক স্বাধীনতার পক্ষের একজন সর্বদা মানুষ। যে কোন জায়গায়, যে কোন পরিস্থিতিতে নিজের মতটি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর অভিমত কখনো মুক্তচিন্তার পক্ষে গেছে, কখনো সাম্প্রদায়িকতার পক্ষেও গিয়েছে। তবে তিনি এই পক্ষাবলম্বনে ক্ষেত্রে কখনোই কুটিলতার আশ্রয় নিতেন না। রাখঢাক করতেন না।
তাই তাঁর জন্মের শত বছর অতিক্রান্তের ও পরআমরা খুব সহজে তাঁকে ব্যাখ্যা করতে পারছি, বিশ্লেষণ করতে পারছি।থাঁকে নিয়ে সাবলীল ভাবে ভাবতে পারছি।
মনীষী আবুল ফজলের রচনাবলীর শিরোনামগুলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনীসহ বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০), মাটির পৃথিবী (১৯৪০), বিচিত্র কথা (১৯৪০), রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭), রেখাচিত্র (১৯৬৬), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২) তার অন্যতম রচনাবলী।
বাংলাদেশের শিক্ষা ও সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখায় একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননার পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবুল ফজলকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। তাঁর পুরষ্কার প্রাপ্তির তালিকা বেশ দীর্ঘ। বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩)( পাকিস্থান আমলে) , আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮০), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), আবদুল হাই সাহিত্য পদক (১৯৮২) এবং সর্বশেষ সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১২ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।
১৯৮৩ সালের ৪ মে বার্ধক্যজনিত কারণে জন্মভূমি চট্টগ্রামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।হয়তো খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি শেষ জীবনে তাঁর এই প্রগতিশীল শিবির আর ধর্মান্ধ শিবিরের ভিতরে দ্বৈত অবস্থানের জন্যে।